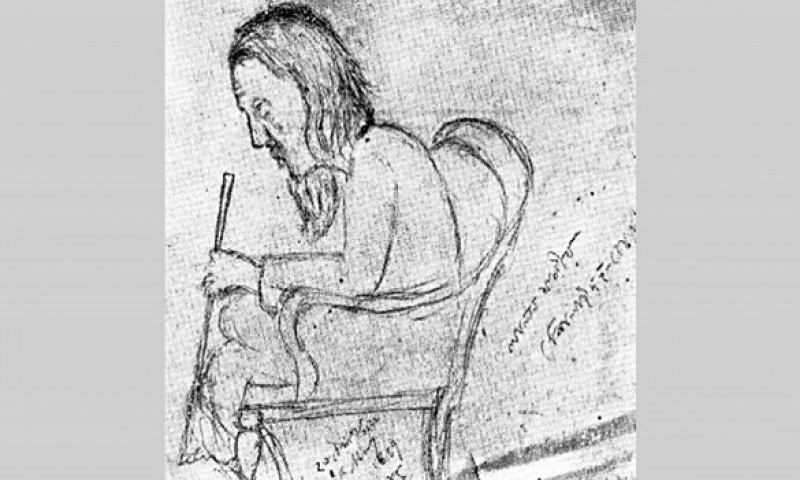
ছবি সংগৃহীত
মিলন সরকার : লালন বিষয়ে আমাদের সামান্য পঠন-পাঠনে মনে হয়েছে যে, প্রায় সবাই লালনকে বাইরে থেকে দেখেছেন। আমাদের মনে হয় তাঁকে ভেতর থেকে দেখা দরকার। চলতি ইতিহাস তো কর্তৃত্বশালীদের নির্দেশিত। ইতিহাসেরও বিপরীতক্রম আছে, কথার ভেতরেও কথা থাকে। ইতিহাসের, কথার সেই নেপথ্যকথাটি ধরবার এ চেষ্টা। এ সব গানের অন্তরশায়ী অর্থকে কল্পনাশ্রয়ী করে তোলা হয়েছে বলে একে একেবারে প্রত্যাখ্যান করবেন না আশা কারি। লালনবীক্ষণে আমাদের এই প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতাকে সহৃদয় পাঠকেরা সহজভাবে নেবেন আশা করি।
১৯১৫ সালে ‘প্রবাসী’তে মুদ্রিত লালনের ‘খুলবে কেনে সে ধন ও তার গাহেক বিনে’ এ গান আজ আমাদের এ লেখার শিরোনাম। এ গানে লালন বলেছেন যে, যে বোঝে কেবল তার কাছেই কথার মানে ধরা দেয়।
১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালনের মৃত্যুর ১৪ দিন পর ৩১ অক্টোবর হিতকরী পত্রিকা তদানীন্তন নদীয়া, এখন কুষ্টিয়া জেলাধীন ছেঁউড়িয়ায় লালন শিষ্য শীতল প্রমুখের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাতে জানা যায় যে, তিনি কায়স্থ, চাপড়ার ভৌমিকেরা তাঁর জ্ঞাতি, তীর্থে যাবার পথে সম্ভবত গুটি বসন্তে আক্রান্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে এক মুসলমান তন্তুবায় ঘরে সেবা ও চিকিৎসা পান, সম্ভবত তখন ঐ বাড়ির অতিথি ফকির সিরাজ সাঁইয়ের কবিরাজিতত্ত্ব, তাঁর কাছে কিছু তত্ত্বকথা ও ফকিরি গানও শুনে থাকবেন। লক্ষণীয় যে, তিনি নিশ্চল সামন্ত কৃষিনির্ভর উৎপাদক পরিবারের সন্তান, তন্তুবায় গৃহে অবস্থানহেতু হস্তশিল্পের সচল উৎপাদন প্রকৃতির দৃশ্য তাঁর চিত্তজগতের স্থাণুত্বকে সম্ভবত নাড়া দিয়েছিল, তিনি খুব ধার্মিক, সংসারী, তাঁর বাউল জীবনের স্ত্রী ও ধর্মকন্যা এবং কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ছিল, তিনি পরশ্রমজীবী ছিলেন না, জীবিকার লক্ষে সম্ভবত কচু ও পানের চাষ করতেন এবং কবিরাজি চিকিৎসা দিতেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর ইত্যাদি এবং সেই সাথে লালনের একটি গান (সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে) ছাপা হয়েছিল। লালনের গানের ভনিতায় নালন তথা লালন নামটি লালনের পরিবারপ্রদত্ত না তাঁর বাউল জীবনে গৃহীত তা জানা যায় না।
১৮৭২ সালে কাঙালের গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় লালনের নাম প্রথম জানা যায়। অনুমান করা যায় যে, বছর তিরিশেক বয়সের দিকে অর্থাৎ অনুমান ১৮০০ এর দিকে তিনি মুসলমানগৃহে অন্নজলগ্রহণের অপরাধে রক্ষণশীল সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন এবং তাঁর নাম পরিচিত হয়ে উঠতে অন্তত বছর তিরিশেক অর্থাৎ অনুমান ১৮৩০ পর্যন্ত সময় লেগেছিল।
মাঝখানের অর্থাৎ ১৮৩০-৭২ পর্বের ৪২ বছর সম্ভবত গুরুর আশ্রয়ে এবং ভ্রাম্যমান জীবনে কাটিয়েছেন তিনি। সেই ১৮৭২ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকে লালনের কথা লিখে চলেছেন। তার ৮ বছর পরই ১৮৮০ তে কাঙালকুটিরে লালনের গানের (আমি একদিনও না দেখিলাম তারে) প্রথম আসর বসবার কথা জানা যায়, ১৮৮৫ সালে কাঙালের ব্রহ্মা-বেদে তাঁর গান (কে বোঝে সাঁইয়ের লীলাখেলা) প্রথম ছাপা হয়। আবার মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৮৯-এ শিলাইদহে বোটের ওপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি গান শোনাতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেই ১৮৮৫ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর গান নিয়ে কাজ হচ্ছে, লেখা হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা ও পাঠান্তর। ইদানীং তাঁর গানের মর্মোদ্ধারে শব্দভেদী এমনকি শব্দবেধী ভাষ্যও রচিত হচ্ছে। তাঁর গানের ধরন-ধারণ নিরিখ যাচাই করে তার আবার নানান ভাগও করা হচ্ছে, শব্দের ব্যবচ্ছেদও হচ্ছে। কিন্তু তাঁর গানের কাল অর্থাৎ কোন গান আগে, কোন গান পরে রচিত, একথা ঠিক করে বলা মুশকিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর ভনিতাবিহীন গানগুলো তাঁর গুরুধরার আগে রচিত বলে মনে হয়। কতকগুলি গানের ভনিতা দ্ব্যর্থবোধক বিধায় কেউ কেউ মনে করেন তা সিরাজরচিত।
বাংলার ভয়ংকর প্রাণঘাতী মন্বন্তর হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের ১৩ বছর পর ১৭৭০ সালে। তার ৪ বছর পর ১৭৭৪ সালে লালনের জন্ম, সম্ভবত পিত্রালয় তদানীন্তন যশোর, পরে নদীয়া, এখন কুষ্টিয়া জেলাধীন ভাঁড়ারায় নয়, সেকালের নিয়মে মাতুলালয় পাশের গ্রাম চাপড়ায়। তখন বাংলার দুর্দিন; খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, সীমাহীন দারিদ্র ও বেকারত্বের মুখোমুখী বিব্রত মানুষ। লালনের বয়স যখন ১৯, সেই ১৭৯৩ সালে, যখন লুণ্ঠনসর্বস্ব ইংরেজ কোম্পানির শাসন নতুন জমিদারি প্রথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করল তখন জমিদারতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা এবং তার সাথে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের চরম অমানবিকতা মানুষের নাভিশ্বাস ডেকে এনেছিল। তাঁর বয়স যখন ১৮, তখন গঞ্জশহর কুমারখালীতে বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠছে, ওখানে ১৭৯২ সালে এক রেশম কুঠিতে দাবী আদায়ের লক্ষে শ্রমিক বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেপাইরা গাদা বন্দুক ব্যবহার করছে। তাঁর জীবৎকালে বাংলার সমাজজীবনে ঘটেছিল নানান আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং সেসবের পরোক্ষ প্রভাব তাঁর চরিত্রে সম্ভবত রেখাপাত করেছিল। দরিদ্র সংসারের নিরক্ষর, না-খাওয়া, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ লালন, ঘরে বিধবা মা ও বধূ, তিনি তো কুমারখালীর কোনো এক কুঠিতে যোগ দিতে পারতেন জীবিকার অন্বেষণে। সম্ভবত উদাসীন প্রকৃতির এ কিশোরকে ঘরে বাঁধবার জন্য অভাবী বিধবা মা বেকার অল্প বয়সী লালনের বিয়ে দিয়েছিলেন, তবু ঘর লালনকে ধরে রাখতে পারেনি। নদীয়ার সংকীর্তনপ্রধান নিমাইচৈতন্য ভাবাশ্রিত নিম্নবঙ্গের এক গণ্ডগ্রামের কিশোরের মনে জেগেছিল বৈরাগ্য ভাবাবেগ, তাছাড়া গ্রাম গ্রামান্তরের সাধু বোষ্টমদের সাথেও হয়তো লালনের ওঠাবসা ছিল। এ সবই লালনের উদাসীন মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রেখেছিল, যৌবনে ঘরে কিশোরী বধূ রেখে তাঁর তীর্থযাত্রাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।
হিতকরীর উল্লেখে জানা যায় যে, তাঁর জন্ম হিন্দু ঘরে। শাস্ত্র তাড়ানো, সমাজ খেদানো লালন মুসলমান ফকির ঝিনাইদহের হরিশপুরের পেশায় পালকি বাহক সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর পূর্বজ্ঞাত হিন্দুঐতিহ্য ও সিরাজসান্নিধ্যহেতু এবং মুসলমান স্ত্রী ঝিনাইদহের হরিশপুরের জমির খোনকারের কন্যা বিসখা বিবির সাহচর্যহেতু মুসলমানঐতিহ্য সহযোগে এক যুগলবন্দী ঐতিহ্যের গান বেঁধেছিলেন। তাঁর গানের উৎস যাই হোক না কেন তিনি না-হিন্দু, না-মুসলমান- তিনি নাড়ার (সন্তানাদিহীন) ফকির। তবে তাঁর গানের মূল প্রবাহ হচ্ছে অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর গান কত? ১৯০৭-১২ সময়কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যে ৩টি নকলী খাতা সংগ্রহ করেন, তার গান সংখ্যা পুনরাবৃত্তি বাদে ৪২৯। এছাড়াও তাঁর আরও অনেক গান আছে। এসব গান তাঁর সাক্ষর শিষ্যরা লিখে রাখতেন, তিনি নিজে সাক্ষর ছিলেন কি-না, জানা যায় না।
আমরা লালন বিশেষজ্ঞ নই, লালন জীবনী তো নয়-ই, এমনকি তাঁর গানের বিশ্লেষণের অধিকারীও নই। আমরা শুধু তাঁর গানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে লালনকে চিনে নেবার চেষ্টা করব। লালনের গানেরও নেপথ্য কাহিনী আছে আবার তাঁর গানের লক্ষ্যও আছে নিশ্চয়ই। আপাতত এতদিনে অন্তত এইটুকু বোঝা গেছে যে, এ এলাকায় লালন নামে অনেক আগে একজন প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁকেই লোকে বলে থাকে বাউল ফকির লালন সাঁই। এখন প্রশ্ন এসে যায়, বাউল কে? প্রতিবাদ কিসের?
জীবন-জীবিকার অভাবে অধিকারবঞ্চনার শিকারে পরিণত তৃণমূল মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে, তার মধ্যে এক ধরনের বিবাগী মনোভাব গড়ে উঠতে পারে অথবা সে উৎকণ্ঠায় উন্মাদ হয়ে যেতে পারে, হতে পারে উচ্ছৃঙ্খল অথবা আত্মঘাতী আবার উন্মূল, এ অবস্থায় সে হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ হতে পারে প্রচণ্ড, আক্রমণাত্মক অথবা তার নিঃস্বতার, রিক্ততার প্রতিকারের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে আপোসহীন বেদনার গানে। মর্মের সেই বেদনাঘন গানই মরমী গান। আর এর রচয়িতা ও গায়ক সেই সব হারানো সব খোয়ানো মানুষ, যাকে আমরা বলে থাকি খ্যাপা, পাগলা বা বাউল। এককালে আমাদেরই হঠকারিতায় লালন ঘর ছেড়ে ছিন্নমূল হতে বাধ্য হয়েছিলেন, সম্ভাবনাময় তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে তিনি বঞ্চিত। কালের কী পরিহাস, এতকাল পরেও, আজও সেই ছিন্নমূলের গানই আমাদের দৃঢ়মূল হতে শেখাচ্ছে।
এবার ঐ প্রতিবাদের কথা। বাউলরা তো ইহবাদী, তাঁদের মধ্যে পারমার্থিকতা থাকার কথা নয়। দুর্লভ এই জীবনেই তাঁদের সব পেয়েছির শেষ। তাঁরা বাধ্য হয়েই প্রচলিত সমাজ বহির্ভুত, অথচ তবু কেন তাঁদের গান আমাদের প্রচলিত সমাজে সমাদৃত? তা কি কেবলই আমাদের মনোরঞ্জনের হুজুগে, না কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনে? তাঁদের গান ইঙ্গিতময়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁরা একটা কথাই বার বার বলতে চেয়েছেন, তাঁরা কেন আজ সমাজছুট আর আমরাই বা কোন ঝুটা সত্যের পেছনে ছুটছি।
জাতপাত প্রথা তো কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করে শ্রেণিশোষণকে বলবৎ রাখার কৌশল। জাতপাতের বালাই বাদ দিয়ে, ধলা কালার ভেদ তুলে দিয়ে, নারী পুরুষের ভাগাভাগি না এনে, ধর্মসাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সকলে মিলে মিশে দুর্লভ ও সংক্ষিপ্ত এ জীবনে সমতার ভিত্তিতে উপভোগের সুযোগ সৃষ্টিতে আমাদের যে অপদার্থতা ও ব্যর্থতা তারই বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ।
আমরা বলে থাকি, মানুষের শেকড়ের খবর আছে লোকসংস্কৃতির ভেতরে। বাউল গান ঐ লোকসংস্কৃতির জোরালো উপাদান। গানই সংস্কৃতির সহজ মাধ্যম যা মানুষকে জাগাতে শতভাগ সক্ষম। সুতরাং বাউল গান, মানবতার গান, সর্বহারা মানুষের গান, আমজনতার জাগরণের গান। এ গান প্রেরণা দেয় সব ভেদ ভুলে গিয়ে, আর্থসামাজিক সমতা এনে সকলে মিলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে অন্তত সহনশীল এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।
প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, লালন জীবনবাদী নন কেননা সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে তো তিনি শ্রম বিক্রি করে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারতেন। লালন মাঠে চোর মঠে সন্ন্যাসী ছিলেন না। মুখে এক আর জীবনে অন্য বা সুবিধাবাদী অর্থাৎ অন্তত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের সেবাদাস ছিলেন না তিনি। ১৮ শতকের সত্তর দশকে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামদেশে তখন বৈষ্ণবীয় বৈরাগ্য ভাবাবেগ প্রবল এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গুরুর সুফি মতাদর্শের মানুষে মানুষে ভাই ভাই তত্ত্ব। এসব আবেগ এবং অর্থনৈতিকভাবে থতমত নিম্নবিত্তের মানুষের যে মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলেছিল তাতে তিনি যে জাতপাতহীনতার অশ্রেণিক একটি বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন তার একটি সামাজিক ইতিবাচকতা ছিল। অন্ততপক্ষে তিনি প্রথাগত সাধক সেজে মতলববাজ সমাজের সাথে সমঝোতা করেননি।
সেকালে যখন আদিম সাম্যবাদী সমাজের পড়তিদশা, প্রভুত্বকামী রাজকীয় সমাজের উঠতিপর্ব তখন সামাজিক অনিশ্চয়তার মুখে এসেছিলেন সংঘবার্তা (প্রতীত্যসমুৎপাদ) নিয়ে মানবমৈত্রীর অগ্রদূত গৌতম বুদ্ধ, আমাদের সাংস্কৃতিক মধ্যযুগে যখন শাস্ত্রীয় জটিলতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরমে তখন এলেন ভক্তিধর্মের সন্তকবির দাদু, কবীর, রজ্জবেরা; তাঁরাও মিলনের বার্তা নিয়ে এলেন। ষোড়শ শতকে আবার অবক্ষয়, অনিশ্চয়তা এবং বহিরাগত অভিঘাত এসে হানা দিলে এলেন নদীয়ার নিমাইচৈতন্য সেই একই জাতপাতহীন সর্বমানবীয় বার্তা (অচিন্ত্যভেদাভেদ) নিয়ে, এভাবে বারবার ভাববিপ্লবীরা চেষ্টা করেছেন সব মানুষের মহাসম্মেলনে এক মানবসমাজ গড়ে তুলতে। কালের করালগ্রাসে ক্ষীয়মান সেই ধারাতেই মহামিলনের বরপুত্র লালন নতুন স্রোতোবেগ নিয়ে এলেন ‘মনের মানুষের’ বার্তায়। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এভাবে বারে বারে শুভবার্তা নিয়ে এসেছেন সমাজহিতৈষীরা অভিন্ন এক মানবমঞ্চ গড়তে।
বলা হয়ে থাকে যে, গানই নাকি এঁদের ভৌত জীবনের বাণী। তাঁদের আসন আসব ও আসঙ্গ একত্রে লালনদর্শনের একটি স্থূল চিত্র মাত্র। লালন তো অন্তত ভানকারী ছিলেন না, তাঁর দর্শনের আরেক পিঠে তো আছে তাঁর গানের যে জোর ও ঝোঁক- যা দ্রোহ এবং মানবতার সপক্ষে মানবতার বিরোধের বিপক্ষে লড়াই, লালনদর্শনের এই যোগ্যতাটুকু মনে হয় বেঠিক নয়। আজকের দেউলিয়া সমাজে যেখানে মানুষ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে সেখানে লালনের গান সেই আপনার খবরের গান।
প্রশ্ন উঠতে পারে, লালন কি সচেতনভাবে তাঁর এসব গান বেঁধেছিলেন? আমাদের উত্তর, নিশ্চয়ই তাই। আমাদের মতো দূর থেকে নয়, খুব কাছ থেকে লালন মুষ্টিমেয় মানুষের তৈরি নিগড়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিগ্রহকে দেখেছিলেন, তাছাড়া তিনি নিজেও সামাজিক অবিচারের সাক্ষাৎ শিকার হয়েছিলেন। শ্রেণিবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, বিশেষ করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের অমানবিকতা তাঁকে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল, তিনি হয়ে উঠেছিলেন দ্রোহী। যেহেতু তিনি স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী মানুষ এবং যেহেতু তিনি সশস্ত্র লড়াকু নন, সেহেতু এসব আর্থসামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি, বেছে নিয়েছিলেন লোকায়ত সুরের গান। তাঁর ভাষাকে নিরাপত্তার কারণে করেছিলেন কৌশলগত আর এভাবেই গানের মাধ্যমে মানবাধিকার বঞ্চিত মেহনতি মানুষের ইজ্জত আদায়ের আহ্বান জানিয়ে গেছেন তিনি। নগরবাসী বর্ণ/ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সমাজসংস্কারের আন্দোলন নয়, হীনস্থানিক জাতপাতহীন গণমানুষের কল্যাণব্রতী তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনের কথাই তিনি বলেছেন তাঁর গানে।
লালনের গানের এই আহ্বানের দিক, প্রেরণার দিক এবং গণজাগরণের এই দিকটি অনুধাবন না করে আমরা কেবলই মনোরঞ্জনের বা অবসর বিনোদনের প্রায়োগিক দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছি। লালনের গানের যে বার্তা শ্রোতার পক্ষে তার অন্তর্ভেদের অক্ষমতা বা করুণ উপেক্ষাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। তিনি তো জটিল অর্থনীতির ভেদাভেদের শিকার নিরুপায় ও জীবিকার অভাবে বিব্রত আমজনতার অস্তিত্ব বিরহের কথাই বলেছেন।
এবারে লালনের ক’টি গানের মূলভাব নিয়ে কিঞ্চিৎ দৃকপাত করা যেতে পারে। যতরকম শব্দ ও ভাব দিয়েই আড়াল করা হোক না কেন, ভাবোর্ধ্ব বাস্তবতা লক্ষণীয়। তুলনার খাতিরে পাশাপাশি মূলগানগুলো উল্লেখ করা হলো।
১. কাঙাল কুটিরে লালনের গাওয়া গানগুলোর একটি:
আমি একদিন না দেখিলাম তারে।/ আমার বাড়ীর কাছে আর্শিনগর এক পরশি বসত করে ॥/ ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই/ কিনারা নাই তরণী পারে; মনে করে,/ দেখব তারি, আমি কেমনে সেথা যায় রে ॥/ আমি বল্ব কি পরশির কথা, ও তার/ হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে, সে/ ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥/ পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা/ সকল যেত দূরে; আবার সে আর লালন/ একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক ॥
‘আমি’ বাস্তব সমাজজীবনে অস্তিত্বের প্রশ্নে ইতিবাচক কোনো জীবিকার সন্ধানে নিরুপায় মানুষ কোনদিন খুঁজে পায় না সেই ‘তারে’ নিশ্চিন্ত জীবন। জীর্ণ কুঁড়েঘরের পাশেই সেই ধনাঢ্য সমাজ নিয়ন্তার সৌধ, ধরা ছোঁয়ার বাইরের সেই প্রতিবেশি সুখ স্বাচ্ছন্দে বাস করে। যতদূর তাকানো যায় তাদেরই দৌরাত্ম্য, এদের কূট কৌশলের কোনো সীমা নেই, তা উত্তরণের কোনো উপায়ও নেই। সেই নিশ্চিন্ত ঠিকানায় কী করে যাওয়া যায় সেকথাও ভাবা হয়েছে। দোর্দ- প্রতাপান্বিত সেই সমাজপতির কথা কি আর বলা যায়, তার ক্ষমতার বলয় এত প্রবল যে তার সীমা সরহদ্দ করা দুষ্কর। তাদের কী মতি তা বোঝা দায়। কখনো মনে হয়, এই বুঝি তাদের স্বরূপ, কিন্তু পরক্ষণে দেখা যায় তা অন্যরূপ। তাদের প্রতাপ প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা নির্ণয় অসম্ভব। ঐ প্রতিবেশি যদি গরিব মানুষের মতো দুঃখভারক্লিষ্ট অধিকারবঞ্চিত মানুষ হতো, তবে তার সাথে সহমত হওয়া যেত বা তাকে সহযোদ্ধা হিসেবে পাওয়া যেত। একই সমাজে তার আর গরিষ্ঠ দরিদ্রজনের অবস্থান অথচ উভয়ের মধ্যে যে বিপুল ফারাক- সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে দূরত্ব তা এত দুস্তর যে নাগালের বাইরের এ শত্রুকে উৎখাত করা অসম্ভব। খেটে খাওয়া মানুষের এই যে উদ্বৃত্ত শ্রম, তার পাহাড় জমানো পিরামিডের শিখরচারী ঐ পড়শীকে কি করে পিরামিডের তলদেশের সেই অধিকারবঞ্চিত জন লড়াই করে পরাস্ত করবে?
সুতরাং এ গান অধিকার বঞ্চনার আহাজারির প্রতীক।
২. কাঙালের ব্রহ্মা-বেদে মুদ্রিত গানটি :
কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা খেলা; সে যে, আপ্নি গুরু হয়, আপ্নি চেলা ॥/ সপ্ত তলার উপর সে, নিরূপ রয় অচিন দেশে, প্রকাশ্য রূপ লীলা/ বাসে, চেনা যায় না লেগে বেদের খেলা ॥/ অঙ্গের অবয়বে সৃষ্টি, করিল সে পরমেষ্টি, তবে কেনে আকার নাস্তি,/ বলে না জেনে সে ভেদ নিরালা ॥/ যদি কারু হয় চক্ষুদান, সেই দেখে রূপ বর্ত্তমান, লালন বলে তার/ জ্ঞান ধ্যান হবে দেখিয়ে সব পুঁথির পালা ॥
‘সাঁই’ স্বার্থান্বেষী মহলের তৈরি করা কৃত্রিম অর্থ সংকট এবং ‘লীলাখেলা’ অর্থাৎ সেই সংকটের সৃষ্ট বিচিত্র অস্থিতিশীলতা। আর এই কৃত্রিমতার অবস্থান এত তুঙ্গে যে তা সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। আর সেই শক্তি যার আধিপত্যের প্রকাশ সদা চঞ্চল ও ছলনাপূর্ণ, অথচ বিত্তশক্তি কখনো নৈর্ব্যক্তিক, কখনো বা ব্যক্তিক, এই কৌশল এত গভীর যে কেতাবি বিদ্যায় তা আয়ত্ব হয় না, কৌশলী মানুষই এর রহস্য জানতে পারে।
সামন্ত অর্থনীতির শিকারে পর্যদুস্ত, দুরবস্থার কার্যকারণ নির্ণয়ে অজ্ঞতাহেতু অসহায়ত্বের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এ গানে।
৩. হিতকরীতে মুদ্রিত গানটি:
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,/ লালন ভাবে জাতের কিরূপ দেখ্লেম না এই নজরে।/ কেউ মালায় কেউ তছবি গলায়,/ তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়/ যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়/ জাতের চিহ্ন রয় র্কারে ॥/ যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,/ নারীর তবে কি হয় বিধান,/ বামণ চিনি পৈতা প্রমাণ,/ বামণি চিনে কিসে রে ॥/ জগৎ বেড়ে জেতের কথা,/ লোকে গৌরব করে যথা তথা/ লালন সে জেতের ফাতা/ ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে ॥
‘জাত’ অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের যে অবান্তর বিভেদমূলক ব্যবস্থা, মানুষের ধর্ম পরিচয়ের যে ভেদরেখা অথবা নারী পুরুষের যে লিঙ্গবৈষম্য, এ তো মানুষকে বিভক্ত করার অপকৌশল এবং একে কেন্দ্র করে শ্রেষ্ঠতা এবং হীনতার প্রভেদ তো আসলে সেই ভাগ কর শাসন কর বিভাজনী কূটকৌশল।
‘সবার ওপরে মানুষ সত্য’ এই ব্রত নিয়ে এক কাতারে সামিল হবার আহ্বান এ গানে।
৪. প্রবাসীতে মুদ্রিত গানটি:
খুলবে কেন সে ধন, (ও তার) গায়ক বিনে।/(কত) মুক্তামণি রেখেছে সে ধনী, (সে ধন)/বাঁধাই করে সে দোকানে ॥/সাধু মহাজন যারা, মালের মূল্য জানে তারা,/মূল্য দিয়ে লন অমূল্যরতন, সে ধন জেনে শুনে/তারাই কেনে।/মাখাল ফলের বরণ দেখে, (যেমন) ডালে বসে/নাচে কাকে,/তেমনি আমার মন চটকে বিমন,/(মন তুই) দিন ফুরালি দিনে দিনে।/মন তোমার গুণ জানা গেল, পিতল কিনে সোনা বল,/অধীন লালন বলে মন চিন্লিনে সে ধন,/মূল হারালি (মন তুই) নিজের গুণে।
‘ধন’ অর্থাৎ সেই সর্বজনীন সম্পদ যার ‘মূল্য’ বোঝে সেই আধিপত্যবাদী ‘মহাজন’-কেমন করে তা ‘বাঁধাই’ করে বাজার অর্থনীতিকে কব্জা করা যায় তার বেসাতি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ অর্থনীতির এ কুটিল জটিলতার ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে অসহায়, তারা ঠকে, বঞ্চিত হয় তাদের অধিকার থেকে, এভাবেই চলে লুণ্ঠন দাপট আর জীবনভর ফাঁকিই হয় সাধারণের সর্বস্ব।
এ গানেও সেই অসহায়ত্বের বিদীর্ণবেদনা ধ্বনিত।
এভাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লালনের গানের শাব্দিক নয়, মৌলিক অর্থ উদ্ধারে এগোলে দেখা যাবে তার মূল সুর জীবনবাদী, বৈরাগ্য নয়।
আজকের যে বিশ্বব্যবস্থা, তাতে লালনের গান কতটুকু ইতিবাচক তা বিশেষজ্ঞজন তলিয়ে দেখবেন। তবে লালনের গান শুধু বিনোদন সামগ্রী নয়, নয় শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের উপলক্ষের সংস্কৃতি। গানের ভেতর দিয়ে তাঁর স্বপ্নকে বোঝা এবং তা বাস্তবায়নের কাজটি করা হচ্ছে না। লালনের গানের আদিখাতা সংগ্রহ, গানগুলি সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। এই গানগুলোর যাঁরা ধারক বাহক অর্থাৎ ঘরছাড়া সেই বাউলদের পুনর্বাসনের কাজটিকে আমরা ভুলে গেছি, তাঁদের প্রান্তবাসী না রেখে, পরান্নজীবী না করে, দেহতত্ত্বের হেঁয়ালিপনা থেকে সরিয়ে এনে, শিক্ষা সাম্য প্রগতিমুখী মানুষের কাতারে তাঁদের সামিল করে দুর্লভ ও সংক্ষিপ্তকালের এ সম্ভাবনাপূর্ণ মানবজীবনের পরিপূর্ণতার নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার অঙ্গীকার আজ আমাদের করতে হবে।*
সহায়ক গ্রন্থ:
১. সনৎকুমার মিত্র’র লালন ফকির কবি ও কাব্য (১৩৮৬ কলকাতা)।
২. আবুল আহসান চৌধুরী’র লালন স্মারকগ্রন্থ (১৯৭৪ ঢাকা), লালন শাহ (১৯৯২ ঢাকা), লালনসমগ্র (২০০৮ ঢাকা)।
৩. শক্তিনাথ ঝা’র ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল ও শিল্প (১৯৯৫ কলকাতা)।
৪. সুধীর চক্রবর্তী’র ব্রাত্য লোকায়ত লালন (১৯৯৮ কলকাতা)।
৫. ম. মনিরউজ্জামান’র সাধক কবি লালন: কালে উত্তরকালে (২০১০ ঢাকা), লালনবীক্ষণ জীবন পত্র ও গানে (২০১২ ঢাকা)।
*কৃতজ্ঞতা: ভারত বিচিত্রা, জুন ২০১৭, ঢাকা। [ঈষৎ পরিবর্ধিত]
[মিলন সরকার: প্রবন্ধকার ও গবেষক; অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সিরাজুল হক মুসলিম হাই স্কুল, কুষ্টিয়া।]
এএইচ